মৌলিক বল হচ্ছে এমন সব বল যা সংস্পর্শে ব্যাতীত পরস্পরের মিথস্ক্রিয়ায় একটি বস্তুর অপর একটি বস্তুর ওপর প্রয়োগ করে। চার প্রকার মৌলিক বলের সন্ধান পাওয়া গেছে যথা :
1. মহাকর্ষ বল
আমরা যেসব গ্রহ-নক্ষত্র দেখি, এগুলো সবই প্রায় বৃওাকার পথে গতিশীল বৃত্তাকার গতির জন্য কেন্দ্রমুখী বল প্রয়োজন। গ্রহ গুলোর মধ্যে এক প্রকার আকর্ষণ বল আছে যা প্রয়োজনের কেন্দ্রমুখী বলের যোগান দেয়। মানুষের এ ধারণা বহুদিনের। গ্রহ-নক্ষত্র গুলোর মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বলকে খ- গোলীয় বা জ্যোতিষ্ক মন্ডলীয় বল বলা হত। 1686 সালে বিজ্ঞানী নিউটন দেখান যে শুধু গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যেই নয়,সকল বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে। তিনি বলের নাম দেন মহাকর্ষ বল।
ধারণা করা হয়, মিথস্ক্রিয়াকারি বস্তুসমূহের মধ্যে গ্রাভিটন নামক এক প্রকার ভারহীন কনার বিনিময়ে এ মহাকর্ষ বলের উদ্ভব হয়। বৃহৎ বস্তুসমূহের মধ্যে মহাকর্ষ বল বেশি তীব্র। কিন্তু আপেক্ষিক সবলতার বিচারে বিষয়গুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে দুর্বল বল। তাই ক্ষুদ্র বস্তুসমূহের মধ্যে এ বল তেমন একটা বুঝতে পারা যায় না। দুর্বল হলেও এ বলের ক্রিয়া অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত।
2. তড়িৎ চুম্বক বল
দুটি তড়িৎ চার্জ পরস্পরের ওপর একটি বল প্রয়োগ করে। একে তড়িৎ বল বলে। আবার, দুটির চুম্বক মেরুর মধ্যে একটি বল ক্রিয়া করে, একে চৌম্বক বল বলে। পূর্বে এ দু'টি বলকে ভিন্ন মনে করা হতো কিন্তু পরে দেখা গেল, গতিশীল চার্জ চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে এবং গতিশীল চুম্বক তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে। এমনকি দুটি চার্জের আপেক্ষিক গতি থাকলে পরস্পরের ওপর তড়িৎ ও চুম্বক বল প্রয়োগ করে।
তাই বলা যায় তড়িৎ বল ও চৌম্বক বল একে অপরের সাথে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে গতিশীল চার্জ গুলোর মধ্যে অতিরিক্ত তড়িৎ বলই হচ্ছে চৌম্বক বল। তাই এ দুটি বলকে একএে তড়িৎ চৌম্বক বল বলে। ফোটন নামক এক প্রকার মৌলিক কণিকার বিনিময় এর উদ্ভব হয়। মহাকর্ষ বলের তুলনায় এটি অনেক বেশি সবল, তবুও সার্বিক বিবেচনায় এটি মাঝারি ধরনের বল। মহাকর্ষ বলের তুলনায় এর বিস্তৃতি অসীম পর্যন্ত।
3. সবল বল
কতগুলো ধনাত্মক চার্জযুক্ত কণা প্রোটন ও তড়িৎ নিরপেক্ষ কণা নিউটন সমন্বয়ে পরমানু গঠিত।আমরা জানি,সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। এখন প্রশ্ন হলো, প্রোটনগুলো অতি স্বল্প পরিসরের মধ্যে কিভাবে থাকে? তড়িৎ বিকর্ষণ বলের জন্য দূরে সরে যায় না কেন? নিশ্চয়ই এখানে আরো একটি আকর্ষণ বল নিউট্রন ও প্রোটন কণার মধ্যে ক্রিয়াশীল আছে,যা তড়িৎ বিকর্ষণ বলের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। এ বলই তড়িৎ বলকে পরাজিত করে প্রোটন ও নিউট্রন গুলিকে একত্রিত করে রেখেছে। শক্তিশালী এ আকর্ষণ বলকে সবল বল বলে।
সুতরাং যে আকর্ষণ বল প্রোটন- নিউট্রন তথা নিউক্লিয়ন কণা বা নিউক্লিয়নগুলোকে একত্রিত করে নিউক্লয়াস গঠন করে তাকে সবল বল বলে। এ বল শুধু অতি অল্প দূরত্বে নিউক্লীয়ন গুলোর মধ্যে ক্রিয়াশীল। বলের পাল্লা 10-15 m অর্থাৎ 10-15 m এর অধিক দূরত্ব থেকে তেমন কোন প্রভাব থাকে না। বিজ্ঞানী ইউকাওয়া 1935 সালে দেখান যে, মেসন নামক এক প্রকার মৌলিক কণার বিনিময়ের ফলে এ বলের উদ্ভব। সবল নিউক্লিয় বল মৌলিক বলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বল।
4. দুর্বল নিউক্লিয় বল
সবল বল নিউক্লিয়নগুলোকে ধরে রেখে নিউক্লিয়াস গঠন করে কিন্তু কোন নিউক্লিয়াসে প্রোটন নিউট্রন এর অনুপাত এর স্থায়িত্বের জন্য যথাযথ না হলে একটি নিউট্রন ভেঙ্গে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনে পরিণত হয়। এই ইলেকট্রনগুলোকে বিটা কণা বলা হয় এবং এ ঘটনাকে বিটা ক্ষয় বলে। বিটা ক্ষয়ের জন্য নিউক্লিয়াসের মধ্যে আরও একটি বলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।একে দুর্বল নিউক্লিয় বল বলে।
সুতরাং বলা যায় প্রোটন নিউট্রন এর অনুপাত যথাযথ না হলে অস্থিতিশীলতা বা বিটা ক্ষয়ের জন্য যে বল দায়ী তাকে দুর্বল নিউক্লিয় বল বলে। W ও Z বোসন কনার বিনিময়ের ফলে এ বলের উদ্ভব হয়। এটি স্বল্প পাল্লার বল।এর পাল্লা 10-17 m এবং এর সবলতার সবল বল ও তড়িৎচুম্বক বল অপেক্ষা কম কিন্তু মহাকর্ষ বল অপেক্ষা বেশি।
বলের পাল্লার মধ্যে অবস্থিত মৌলিক কণাগুলোর মধ্যকার বলের মানের অনুপাত দ্বারা আপেক্ষিক সবলতার বিচার করা হয়।
মৌলিক বলসমূহের আপেক্ষিক সবলতা,
সবল বল : তড়িৎ চৌম্বক বল :দুর্বল নিউক্লিয় বল: মহাকর্ষ বল = 1:10-2 :10-5 :10-39
আমরা পূর্বেই দেখেছি,
নিউক্লিয়ন থেকে গ্যালাক্সি পর্যন্ত বিশ্বের সকল ঘটনা ও গঠন বর্ণনায় কনাসমূহের মধ্যে ক্রিয়াশীল চারটি মৌলিক বল - সবল বল,তড়িৎ চৌম্বক বল,দুর্বল বল ও মহাকর্ষ বলই যথেষ্ট। সারণিতে মৌলিক বলসমূহের পার্থক্য দেখানো হলো:
মৌলিক বলসমূহের একত্রিতকরণ সূত্র (Unified theory of fundamental forces)
সময়ের সাথে সাথে মৌলিক বল সমূহের তালিকা পরিবর্তিত হয়েছে। আগে সবল ও দুর্বল সম্পর্কে মানুষের জানা ছিল না। এমনকি মধ্যাকর্ষণ(যা বস্তুসমূহকে পৃথিবীর দিকে টানে) এবং জ্যোতিষ্ক মন্ডলী মধ্যাকর্ষণ (গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে ক্রিয়া করে) গ্যালাক্সি গঠন করে বল দুটি আসলে যে এক সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিলনা বিজ্ঞানী নিউটনের আবিষ্কার এর ফলে এ দুটি বল বিশ্বজনীন মহাকর্ষ বলের রুপ নেয়। তড়িত বল ও চৌম্বক বল একীভূত করে তড়িৎ চৌম্বক বলের রুপ দেন জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল।প্রফেসর আব্দুল সালাম,শেল্ডন গ্লাসো ও স্টিভেন ওয়াইনবার্গ সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে তৈরি তড়িৎচৌম্বক বল ও দুর্বল বল অভিন্ন দেখতে সক্ষম হন। এ একীভূত বলের নাম দেয়া হয তড়িৎ -দুর্বল বল (Electroweak force).
তড়িৎ দুর্বল বল ও সবল বলকে একত্রিত করার প্রচেষ্টা চলছে। ভবিষ্যতে হয়তো এ দুটি বলকে একীভুত করে বৃহৎ একীভূত বল (Grand unified force) পাওয়া যাবে।
তাপ বিকিরণ
তাপের স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়াকে তাপ সঞ্চালন বলে। তাপ সঞ্চালনের বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশল হতে পারে। তাপ সঞ্চালনের পরিবহন ও পরিচালন পদ্ধতি আমাদের পূর্বপরিচিত। আমরা জানি, এ দুটি পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালনের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ মাধ্যম ছাড়া পরিবহন, পরিচলন পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালিত হতে পারে না। কিন্তু একটা উত্তপ্ত বস্তুর খানিকটা নিচে হাত রাখলে উত্তপ্ত অনুভূত হয়। উত্তপ্ত বস্তু ও হাতের মধ্যবর্তী স্থানে বায়ু আছে কিন্তু বায়ু তাপ কুপরিবাহী। এবং পরিচালন পদ্ধতিতে তাপ উপরের দিকে সঞ্চালিত হয় তাহলে নিচের দিকে তাপ আসছে কিভাবে?
তাছাড়া সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অধিকাংশ স্থানই মাধ্যম শূন্য। তাহলে সূর্য থেকে তাপ পৃথিবীতে আসছে কিভাবে?
নিশ্চয়ই তাপ সঞ্চালনের আরো একটি পদ্ধতি আছে। তাপ সঞ্চালনের তৃতীয় পদ্ধতি হলো বিকিরণ। বিকিরণ পদ্ধতিতে উত্তপ্ত বস্তু থেকে তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ রূপে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে এবং কোন মাধ্যম ছাড়াই অতি দ্রুত গতিতে সরলপথে সঞ্চালিত হয় সুতরাং তাপ উত্তপ্ত বস্তু থেকে তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ রূপে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসা এবং দ্রুত গতিতে সরল পথে সঞ্চালিত হওয়ার পদ্ধতিকে তাপ বিকিরণ বলে। বিকিরণ পদ্ধতিতে যে তাপ সঞ্চালিত হয় তাকে বলে বিকীর্ণ তাপ।
একখণ্ড লোহাকে অত্যাধিক উত্তপ্ত করলে তা লাল আকার ধারণ করে। এরূপ একটি উত্তপ্ত লোহাকে অন্ধকার ঘরে রাখা হলে ঘরটি কিছুটা আলোকিত মনে হয় অর্থাৎ উত্তপ্ত লোহা থেকে আলো নির্গত হয় মূলত এই আলো বিকীর্ণ তাপ শক্তির একটি রূপ। শুধুমাত্র দৃশ্যমান আলো নয়, বেতার -টেলিভিশন তরঙ্গ, মাইক্রো তরঙ্গ, অবলোহিত রশ্মি, অতিবেগুনি রশ্মি, X - রশ্মি, গামা রশ্মি প্রভৃতি সবই বিকীর্ণ তাপশক্তি। বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গ তত্ত্ব অনুসারে এ সবই তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ।এদের পার্থক্য শুধু তরঙ্গদৈর্ঘ্যের। গামা রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম, 10-12 m ক্রমের। এর পর X - রশ্মি, অতিবেগুনি রশ্মি, দৃশ্যমান আলো, অবলোহিত আলো, মাইক্রো তরঙ্গ, বেতার টেলিভিশন তরঙ্গ ইত্যাদির তরঙ্গদৈর্ঘ্য পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পায়।
বিকীর্ণ তাপ শক্তি যখন কোন বস্তুর শোষণ করে তখন বস্তু উত্তপ্ত হয়। সকল বস্তু থেকে সব তাপমাত্রায় কমবেশি বিকিরণ হয় এবং পরিপার্শ্ব থেকে নিঃসৃত বিকিরন বস্তুর উপর আপতিত হলে কমবেশি শোষনও করে। বস্তু পারিপার্শ্ব থেকে উত্তপ্ত হলে বস্তু কর্তৃক শোষণ অপেক্ষা বিকিরন বেশি হয় ফলে তা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হতে থাকে এবং বিকিরণের পরিমাণ কমতে থাকে বিকিরণের পরিমাণ কমতে কমতে এক সময় শোষণ ও বিকিরনের পরিমাণ সমান হয় তখন তা আর ঠান্ডা হয়না। বিকীর্ণ তাপ এর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়:
১. বিকীর্ণ তাপ ও তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ আকারে সঞ্চালিত হয়।
২. বিকীর্ণ তাপ সঞ্চালনের জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।
৩. বিকীর্ণ তাপ সরলরেখায় চলে।
৪. এর দ্রুতি আলোর দ্রুতির সমান।
৫. বিকীর্ণ তাপের প্রবাল্য উৎস থেকে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।
৬. উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে বিকীর্ণ তাপের প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন ও সমাবর্তন ঘটে।
0
0
0
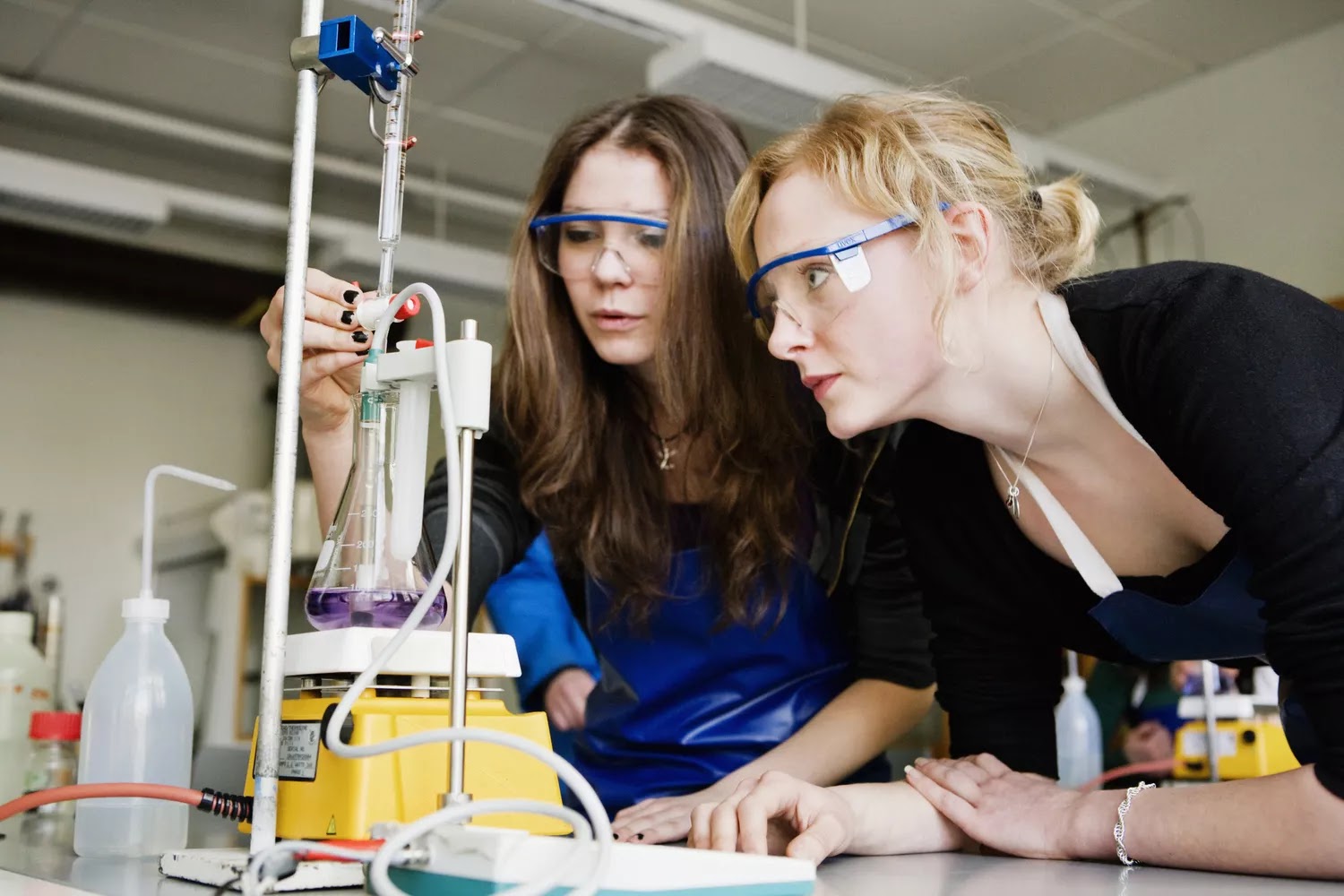









Post a Comment